ট্রাম দুর্ঘটনার আটদিন পর, শম্ভূনাথ হাসপাতাল।
ফাল্গুন। গত একশ’ বছরে কল্লোলিনী তিলোত্তমা কোলকাতায় সংঘটিত একমাত্র ট্রাম দুর্ঘটনায় বুকের পাঁজর ভেঙে, মচকানো উরু আর ভাঙা কণ্ঠী নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি পৃথিবীর নির্জনতম; সম্ভবত তখনও যার মৃত্যুতে কারোই কিছু যায় আসে না — এমনই এক অর্বাচীন — আটদিন ক্রমাগত হৃদযন্ত্রের বিপবিপ সাউন্ড, আর তারপর ম্লান হয়ে যাওয়া নক্ষত্রের মতো নিঃশব্দ পতন — বিশুদ্ধতম, জীবনানন্দ দাশ।
জয় গোস্বামী ‘ব্রিজের ওপরে’ কবিতায় একটা অভাবনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, লিখেছিলেন—
‘কেউ কি মৃত্যুর আগে স্নান করে? / অন্যান্য দিনের মতো সাবধানে সিঁদূর পরে কেউ? / আত্মহত্যা করবে জেনে কেউ কী বাড়ির জন্য মাছ কিনে আনে?’
কেউ কেউ হয়ত করে, কেউ করে না। জীবনানন্দ করেছিলেন। এক অদ্ভুত সন্ধ্যায় দুই হাতে ডাব নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ট্রামের ক্যাঁচারে — স্বেচ্ছামৃত্যু নাকি স্বাভাবিক—সে রহস্য কে জানে, জীবনানন্দ ফিরছিলেন ঘরে। ধর্মতলা থেকে বালিগঞ্জের দিকে ২৪ নম্বর রুটের BOG 304 ট্রামটি রাস্তার মাঝখানের ঘাসের ওপরের ট্রাম লাইন বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। অন্যভূবনের অন্যমনস্ক জীবনানন্দ সম্ভবত পৃথিবীর বাইরের জগতের কেউ। ডায়াবেটিসের জন্য গত কয়েকবছর ধরে দৃষ্টিশক্তিও ঝাপসা হয়ে এসেছিল। ট্রাম আসছে, ঘণ্টা বাজছে অবিরাম, সতর্কবাণী উচ্চারণ করছিল ট্রামের ড্রাইভার, চারপাশের লোকজন চিৎকার করে উঠেছিল; তবু মানুষটির যেন কোনও বাহ্যজ্ঞান ছিল না। আপনমনে রাস্তা পার হচ্ছিলেন— ১৮৩, ল্যান্সডাউন রোডের দিকে, নিচতলার ছোট্ট একটা রুম, চিরদিন না ফেরাদের ঘর। ট্রামের মতো মন্থর নিরীহ যানের নিচে কেউ চাপা পড়তে পারেন, তা তখনও রীতিমতো বিস্ময়কর ব্যাপার। অথচ তিনিই ১৯৩২-এর দিকে ডায়েরিতে লিখেছিলেন ‘How quite possible it may be to slip and runover by tram’. ট্রাম-সংক্রান্ত অবসেশন ছিলো অনেক, লিখেছিলেন—
‘শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন/
জীবনের, জগতের, প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ..’
আসলেই কোলকাতায় এখন ট্রাম-যোগাযোগ প্রায় বন্ধের পথে— সাকুল্যে একটা রুটে চলে। তবু ১৯৫৪ সালে একটা ট্রাম, জীবনান্দের লেখায় যার উল্লেখ এসেছে প্রায়ই, সেই স্থুলযানের নিচেই যবনিকাপতন! যেন সমস্তকিছু আগে থেকেই জেনে জীবনযাপন, আয়নার মতো স্পষ্ট চিত্র— মৃত্যুদর্শন, জীবনেরও অনেক আগে। বিনয় মজুমদার লিখেছিলেন—
‘সংশয়ে সন্দেহে দুলে একই রূপ বিভিন্ন আলোকে
দেখে দেখে জিজ্ঞাসায় জীর্ণ হয়ে তুমি অবশেষে
একদিন সচেতন হরিতকী ফলের মতন
ঝ’রে গেলে অকস্মাৎ, রক্তাপ্লুত ট্রাম থেমে গেল।’
জীবনানন্দ তো সেই অর্বাচীন মানুষ, যিনি জীবনের সমস্ত আনন্দ বিসর্জন দিয়ে কবিতার পেছনে পুরো একটা জীবন লগ্নি করেছেন, খামখেয়ালী কাটালেন বেশিরভাগ সময়ই দারিদ্র্য আর অবহেলা পূঁজি করে। অধ্যাপনা করাতেন বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের ইংরেজি বিভাগে, ছাত্ররা পড়া বুঝতে পারতো না, কাগজ গোল্লা করে ছুড়ে মারতো; বিল্লি ডাকতো। অফিসে গুরুত্বপূর্ণ সব ফাইল ক্রমাগত উধাও হতে লাগলো, পত্রিকার সম্পাদনা করার পর দেখা গেলো সম্পাদক হিসেবে অন্য কারো নাম ছাপলো, টিউশনিতে একদিন না গেলেই বেতন কাটা পড়তো, পত্রিকায় কবিতা পাঠালে লাইনের পর লাইন বাদ দিয়ে ছাপা হতো—কখনো বা ছাপাই হতো না। সামাজিক অবস্থান নেই, কণ্ঠ ভালো না, সন্তান মানুষ করতে পারছেন না; বেতন আটকে যেতো। প্রকাশককে অনুরোধ করতেন কিছু টাকা পাঠানোর জন্য, সাথে দিতেন কবিতা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি। সে কবিতাও লোকে পড়তো না। চাকরি খুঁজতে গিয়ে রাইটার্স বিল্ডিঙে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়া ব্যর্থ সে প্রবাদপুরুষ লিখেছিলেন—‘মানুষের হাতে আজ মানুষ হতেছে নাজেহাল, পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি।’ লিখেছিলেন—‘পৃথিবীতে টাকা রোজগার করতে গিয়ে মূর্খ ও বেকুবদের সাথে দিনরাত গাঁ ঘেষাঘেষি করে মনের শান্তি ও সমতা নষ্ট হয়ে যায়।’
প্রেমিকা চেহারা নিয়ে রসিকতা করতো, দিনের পর দিন দেখা করতে গিয়ে ফিরে এসেছেন ব্যথিত হৃদয়ে। স্ত্রীর সাথেও বনিবনা ছিলো না, মায়ের সাথে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো। সেই বেদনা থেকেই কিনা, জানি না; লিখেছিলেন—
‘মানবকে নয়, নারী, শুধু তোমাকে ভালোবেসে/
বুঝেছি নিখিল বিষ কিরকম মধুর হতে পারে..’
সাড়ে তিন হাজার কবিতা লিখে মারা যাওয়া একজন কবির সাকুল্যে ১৬২টা কবিতা প্রকাশিত হলো জীবদ্দশায় — এমনই পরাজিত জীবনে তাকে বয়ে বেড়াতে হলো নিজেরই নাম ‘জীবনানন্দ’কে। কী প্রহসনই না জীবন জীবনানন্দের সাথে করলো!
জীবনানন্দের বাকি সমস্ত লেখা বাদ দিয়ে যদি শুধু বনলতা সেনকেই তার একমাত্র লেখা গণ্য করি, তবুও এর থেকে তীব্র প্রেম কিংবা করুণার কবিতা দ্বিতীয়টা কি খুঁজে পাওয়া যাবে? আমরা তো জীবনভর পৃথিবীর পথে হেঁটে ফিরতে চাওয়া ক্লান্ত পুরুষ, যার একমাত্র লক্ষ্যই থাকে ঘর, দুদণ্ড শান্তির কাছে শিশুর মতোই ভেঙে-চূড়ে সঁপে দেয়া একটা সহজ জীবন। কবিতায় ‘বনলতা সেন’ চরিত্রটি নিয়ে এক চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন আকবর আলি খান। ‘পরার্থপরতার অর্থনীতি’ বইতে তিনি লিখেছেন, বনলতা সেন ছিলেন বিনোদবালা নামের এক যৌনকর্মী/নর্তকী। এইভাবে কবিতায় উল্লেখিত “দু’দণ্ড শান্তি দিয়েছিল” কথাটির এক নিজস্ব ব্যাখ্যা তিনি দেন। তাঁর মতে “এতদিন কোথায় ছিলেন” কথাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে কবির প্রতি এক বিপন্ন নারীর আর্তনাদ, যে নারীর কাছে দু’দণ্ড সময় কাটানোর পর শেষ পর্যন্ত সব পুরুষকেই ঘরে ফিরতে হয়। এখানে উল্লেখ্য, যৌনকর্মের খদ্দের আকৃষ্ট করার জন্য এই নারীরা প্রায়শই পরিচিত হবার ভান ধরেন। “এতদিন কোথায় ছিলেন?” বলে তারা বোঝাতে চান এই পুরুষটি তার পূর্বপরিচিত এবং তাকে তিনি মনে রেখেছেন। এই তিন শব্দের একটা লাইনের ব্যাখ্যা কতটা ডায়নামিক, অথচ জীবনানন্দ অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে তারে তুলে এনেছেন কবিতায়। বলেছেন, এই হাজার বছর ধরে পথে হাঁটার ক্লান্তি তিনি সঁপে দিয়েছেন বিনোদবালা কিংবা বনলতার কাছে, তার জীবনের যৎসামান্য অর্জন সেই ‘দুদণ্ড শান্তি’ তিনি খুঁজে পেয়েছেন একজন নর্তকীর কাছে!
এই সমস্ত শানে নুযূল কবিতার বুঝতে পারাকে ঋদ্ধ করলেও আমি জীবনানন্দকে ব্যাখাতীতভাবেই বুঝতে চাই, কারণ যখনই তার কবিতাগুলো পড়ে ব্যাখ্যা খুঁজতে যাই, আমাকে কয়েকটা ডাইমেনশন থেকে চিন্তা করতে হয়। মনে হয় এখন যেভাবে ব্যাখ্যা করছি, তারথেকেও ভালো অ্যাঙ্গেল থেকে আলাপ দেয়া যায় কিংবা বুঝতে পারা যায়। তাই এই বুঝতে পারার বোঝা থেকে নিজেকে দূরে রেখে চেষ্টা করি কবিতারে কবিতার মতো থাকতে দিতে। মাত্র ৬২৬টি কবিতায় তিনি কেন দুই হাজারেরও অধিকবার ‘নক্ষত্র’ শব্দটা ব্যবহার করলেন, সেই ব্যাখ্যা আমি খুঁজতে যাই না। আমি শুধু পাঠ করতে থাকি— ‘আমরা হারায়ে যাই, প্রেম তুমি হও না আহত’ আর ‘প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়’ লাইনের স্ববিরোধীতাকে। পাঠ করি—
‘আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন/কতদিন আমিও তোমাকে খুঁজি না’ক’
‘যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ/মরিবার হলো তার সাধ’
‘কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে/সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে’
‘তুমি তো জান না কিছুই/না জানিলে, আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে’
‘মাথার ভিতরে/স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়, কোন এক বোধ কাজ করে’
‘তোমার শরীর— তাই নিয়ে এসছিলে একবার/তারপর মানুষের ভিড় রাত্রী আর দিন— তোমারে নিয়েছে ডেকে, কোনদিকে জানিনি তা’
এইসমস্ত কবিতা, উত্তর-আধুনিক কিংবা কিছু ক্ষেত্রে পরাবাস্তব অনুভূতিকে উস্কে দেয়, মনে হয় এরকম একটা কবিতা শতবর্ষ আগে জীবনানন্দ কীভাবে লিখলেন! তিনি যখন কবিতায় আঁকলেন—
‘মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ/উড়ুক উড়ুক তা’রা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক’
তখন সেই কবিতার লাইনে ‘পৌষের জোৎস্নায়’ কথাটুকু দিয়ে একটা অদ্ভুত আবহ তৈরি করলেন। পৌষের দিকে রাত যখন কুয়াশাবৃত থাকে, তখনকার জোৎস্নার মিশ্রণে তৈরি হওয়া একটা আধিভৌতিক কিংবা অলৌকিক পরিবেশের উল্লেখ তিনি ‘বুনো হাঁস’ কবিতায় করলেন। কিংবা আপনি যখন পড়বেন—
‘বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ/
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি— কুয়াশার পাখনায়—’
শঙ্খমালা কবিতায় অলীক একটা উপমা টেনে কুয়াশায় জুড়ে দিয়েছেন পাখনা। যে-সমস্ত ব্যাপার উত্তর-আধুনিক কিংবা কল্প-সাহিত্যের একান্ত, তা জীবনানন্দ কীভাবে আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে কবিতায় ধারণ করলেন, তা এক বিস্ময়। আকাশলীনা কবিতায় লিখলেন—
‘সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়ো না’ক তুমি/বোলো না’ক কথা অই যুবকের সাথে
ফিরে এসো সুরঞ্জনা/নক্ষত্রের রূপালী আগুন ভরা রাতে’
শেষের লাইনে নক্ষত্রের আলো-কে জীবনানন্দ তুলনা করলেন রূপালী আগুনের সাথে। ঈর্ষাণ্বিত প্রেমিক, যুবকের কাছ থেকে তার সুরঞ্জনাকে কাছে ফিরিয়ে আনার আহ্বানে লুকাতে পারেননি আদি-মনুষ্য অনুভূতি। নক্ষত্রভর্তি রাতকে তার রূপালী আগুন মনে হতে লাগলো। কিংবা ‘বোধ’ কবিতায় দুঃখমিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশের ভঙ্গি, ‘সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা একা কথা কয়!’ আর বিস্ময় পাশে রেখে পরক্ষণেই অনুরাগভর্তি প্রশ্ন রেখে যাওয়া— ‘অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?’ — এই পংক্তিগুলো, এবং অকস্মাৎ পরিবর্তিত অনুভূতি আপনাকে ভাবাবে। পড়বেন ‘ঘোড়া’ কবিতার লাইন — ‘আমরা যাইনি ম’রে আজো— তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়/
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে’
এখানেও দেখবেন সেই জোৎস্নার অদ্ভুত আবহ, অক্টোবরের কুয়াশামিশ্রিত জোৎস্নার প্রসঙ্গ আসছে।
নিজের লেখা কবিতার ব্যাপারে তার ভাবনার কথা পাওয়া যায় ওনারই লেখা চিঠিপত্রে। খুব অন্তরঙ্গ ছিলেন জীবনানন্দ। কবিতা লেখার মতোই খুঁতখুঁতে স্বভাবে আগে চিঠির খসড়া ছাঁচ করে নিতেন, পরে মূল চিঠিটি লিখতেন। ১৯৪৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর প্রভাকর সেনকে লেখা এক চিঠিতে বলেছলেন— ‘ভালো কবিতা লেখা অল্প কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার নয়; কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে সময় লাগে। কোনো কোনো সময় কাঠামোটি, এমন কি প্রায় সম্পূর্ণ কবিতাটিও খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টিলোকী হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপর—প্রথম লিখবার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে-চারদিককার প্রতিবেশচেতনা নিয়ে শুদ্ধ তর্কের আবির্ভাবে কবিতাটি আরো সত্য হয়ে উঠতে চায়।’ ‘কবিতার কথা' নামক প্রবন্ধে ‘বরং লেখনাকো একটি কবিতা’— এর উত্তরে বলেছেন, 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি— কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নবনব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত হয়; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।'
জীবনানন্দের সাথে কবিদেরও বিস্তর যোগাযোগ ছিলো না। রবীন্দ্রনাথের চিঠি অমীয় চক্রবর্তী কিংবা বুদ্ধদেব বসুরা পেয়েছিলেন ঢের, জীবনানন্দের ভাগ্যে জুটেছিলো মাত্র দু’খানা খাপছাড়া চিঠি—তাও যতটুকু না লিখলে ভদ্রতা বজায় রাখা যায় না। সেই অবহেলাবোধ কিংবা সংকোচেই একই শহরে থেকেও কোনোদিন দেখা করতে যাননি রবীন্দ্রনাথের সাথে। তাঁর ভাষায়, 'নিজের জীবনের তুচ্ছতা' ও রবীন্দ্রনাথের 'বিরাট প্রদীপ্তি' দুজনের মধ্যে যে ব্যবধান রেখে গেছে—তিনি (জীবনানন্দ) তা লঙ্ঘন করতে পারেননি। সমসাময়িক কবি হয়েও নজরুলের সাথে কল্লোলের অফিসে একবার মাত্র দেখা হলো। ১৯৩১-৩৪ পর্যন্ত যৌবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ বছরেই তিনি ছিলেন সবথেকে নির্জনতম। চাকরি করলেন না, পত্রিকায় লেখা পাঠালেন না, কোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেও দেখা করলেন না। কোলকাতা ও বরিশালের পথে পথে ঘুরে বেড়ানো এক বোহেমিয়ান জীবনে জীবনানন্দ তখন শুধু পড়লেন আর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে গেলেন। সেই লেখা তাকে অমর করলো কিনা, সময়ের ঊর্ধ্বে নিয়ে গেলো কিনা তা তার পাঠক-সমালোচকরাই খুঁজে বের করুক। আমার জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী জীবনযাপনে সেই অর্বাচীন কবি— জীবনানন্দ দাশ, ছিলেন-আছেন-থাকবেন, একজন নির্জনতম ও শুদ্ধতম হয়ে।
তানভীর আলম রিফাত
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ।
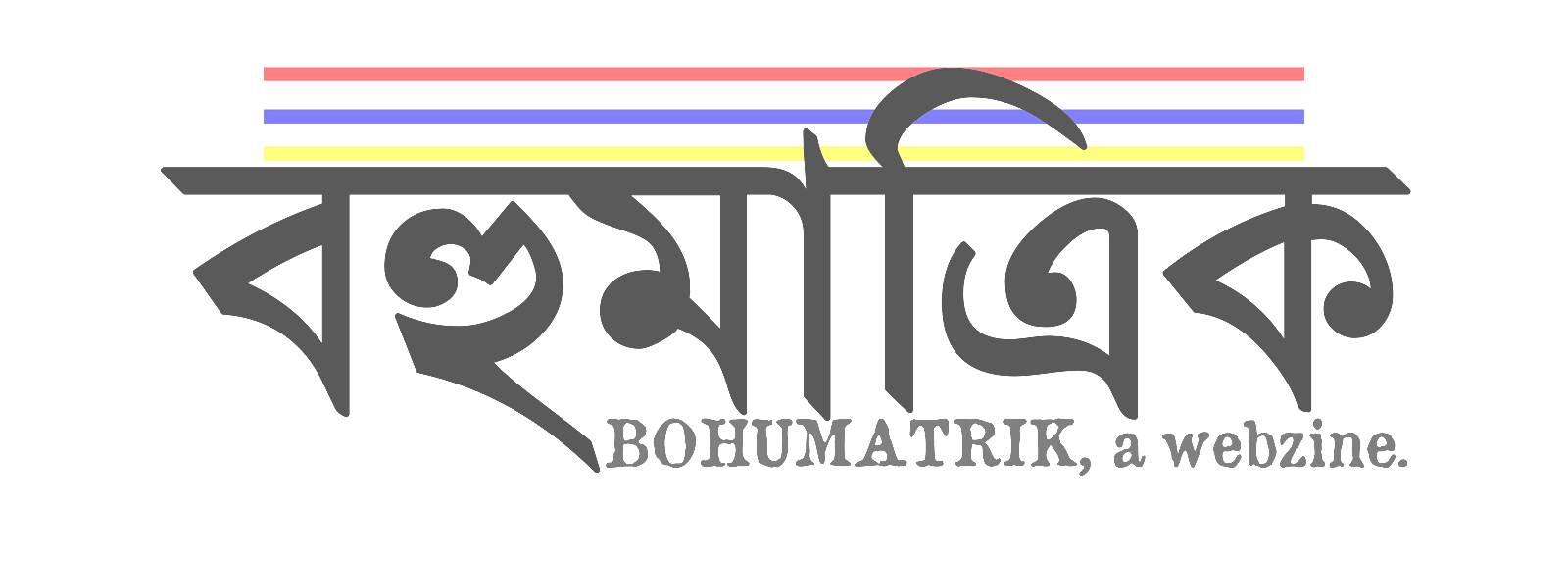
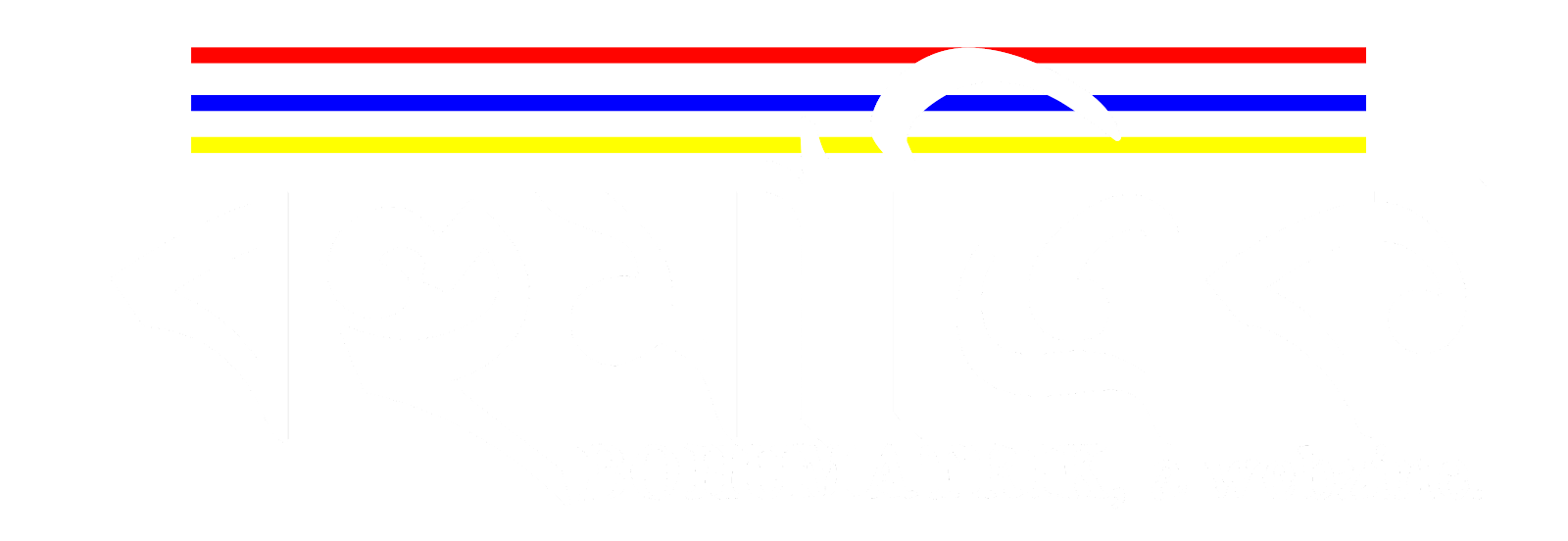
.jpg)




0 Comments